*
রাষ্ট্রবিজ্ঞান যথার্থ অর্থে বিজ্ঞান কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। বিজ্ঞান হল কোন বিষয় সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান ( A body of systematized knowledge)। বিজ্ঞান হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে শৃঙ্খলিত জ্ঞান (Science is a coherent knowledge about some interrelated problems)। কোন বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানী মসকা বলেন যে, “বিজ্ঞান গড়ে উঠে মূলত নিয়মানুগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের বিশেষ ধারার উপর।' বিজ্ঞানের গবেষণায় যে সূত্র ও সত্য আবিষ্কৃত হয় দেশ-কালভেদে তা নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশ্বজনীন নিয়মের (Universal laws) সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি ও অণুর বৈশিষ্ট্য সর্বত্র এক ও অভিন্ন। বিজ্ঞানের কার্যকারণ ও ফলাফলের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই কারণে সর্বত্র একই ফল পাওয়া যায়। পোলানস্কির মতে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণই হল বিজ্ঞানের প্রধান মানদন্ড।'
বিজ্ঞানের উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি পদার্থ বা রসায়ণবিদ্যা যে অর্থে নিখুঁত বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সে অর্থে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বরূপ ও উপাদান এক নয় । একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তু হল কোন বস্তু বা পদার্থ। কিন্তু একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়বস্তু হল সমাজবদ্ধ মানুষ ও রাষ্ট্র। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ, প্রবণতা ও নৈতিকতা ভিন্নতর হয়ে থাকে। মানুষের আচরণকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সূত্রের মধ্যে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ জন্য অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্ভাব্যতার (Science of Probability) বিজ্ঞান বলে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে ন্যায়-নীতির মানদন্ডে বিচার করা হয়। মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্র, স্থিরতা এবং ফলাফলের যে অভিন্নতা তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাওয়া সম্ভব নয়। একথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে পদ্ধতিগত ও নীতিগত যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন ধারাবাহিক তুলনামূলক আলোচনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বহুলাংশে স্থির ও নির্ভুল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ফাইনার বলেন, 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত ভবিষ্যৎ বক্তা না হলেও সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ বক্তা হতে পারি' (In political Science we can become the prophets of probable not the seers of the certain)। ইতিহাসের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়। এরিস্টটল ১৫৮টি সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রের নীতিমালা, আইনের স্বার্বভৌমত্ব এবং বিপ্লবের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা আজও কার্যকর।
তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শাস্ত্রটিকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করতে সাহায্য করেছেন এজন্য তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।
সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলী ইতিহাসের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আবিষ্কার করতে সক্ষম। বিজ্ঞানের পদ্ধতি, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দৃষ্টিকোন থেকে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করতে পারি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অংকশাস্ত্রের মত স্বতঃসিদ্ধ সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, ' রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করি এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎবাণী করে থাকি' (We deal with tendencies, we predict upon the basis of experience)। লর্ড ব্রাইস বলেন, ' যেভাবে আমরা আবহাওয়া বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলি, সেভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকেও বিজ্ঞান বলতে পারি ।' আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের সকল ভবিষ্যৎবাণী যেমন সত্য হয় না, তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎবাণী দেশ, কাল ও ঘটনা চক্রে সবসময় সঠিক হয় না। তার মতে, 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি প্রগতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও গতানুগতিকতার পরিবর্তে অধিকমাত্রায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছেন। পরিসংখ্যান ও গাণিতিক তত্ত্বের মাধ্যমে অর্জিত আচরণগত গবেষণালব্ধ জ্ঞানভান্ডার রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বহুলাংশে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছেন
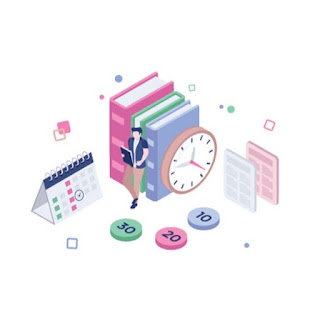
Comments
Post a Comment