*
রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায় কিনা এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদি গুরু দার্শনিক এরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি রাষ্ট্রসম্পর্কিত সামগ্রিক আলোচনাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছেন। পরবর্তী যুগে এই ধারণার সমর্থকদের মধ্যে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা হলেন- সিজউইক, লর্ড ব্রাইস, হবস, বদিন, মন্টেস্কু, বন্টুসলি, ম্যাকেয়াভেলী, উইলোবী, বারজেস, ক্যাটলিন, জর্জ পোলক প্রমুখ দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তাঁরা বিজ্ঞান বলে আখ্যা দিয়েছেন।
জার্মান চিন্তাবিদ হলজেনডরফ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, 'জ্ঞানের ব্যাপক বিস্তার লাভের ফলে রাষ্ট্র সংক্রান্ত সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, ঘটনা ও প্রজ্ঞাকে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিরোনামে অভিহিত করা যুক্তিসঙ্গত।'
অপরপক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়। এদের মধ্যে বাকলে মেটল্যান্ড, এ্যামস ও কোঁতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এসব চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে মেনে নিতে রাজী নন।
মেটল্যান্ড বিদ্রুপ করে বলেন, 'যখন আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিরোনামে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখি তখন প্রশ্নগুলোর জন্য নয় বরং শিরোনামের জন্য দুঃখিত হই।' (When I see a good set of examination questions headed by the word political science, I regret not the questions but the title.') কৌতে প্রধানত তিনটি কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলতে রাজী নন। যথা:-
১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা সম্পর্কে একমত নন;
২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতিতে কোন ধারাবাহিকতা নেই;
৩। ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কোন সঠিক নির্ভরযোগ্য স্থায়ী সূত্র বা মান নেই ।
এ্যামস উল্লেখ করেন ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি এত ব্যাপক ও জটিল যে, তা আলোচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এসব যুক্তির বিপক্ষে ফ্রেডরিক পোলক বলেন যে, 'যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করতে চান না প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ ।
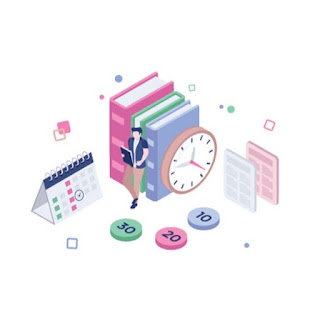
Comments
Post a Comment