*
সাধারণভাবে রাষ্ট্রতত্ত্ব বা রাষ্ট্রীয় মতবাদ বলতে কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ চিন্তাবিদের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণাকে বুঝায় । বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে গৃহীত বহু রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political theory) রাষ্ট্র, ক্ষমতা, রাষ্ট্রের আদর্শ শাসন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে নতুন নতুন তত্ত্বের জন্মের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র উর্বর হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আদর্শ, রাষ্ট্রের ক্ষমতা, আইন ও শাসন পদ্ধতি প্রভৃতির উন্নতি সাধন কল্পে উদ্ভাবিত মতবাদকে রাষ্ট্রতত্ত্ব বলা হয়।
গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিষ্টটলের ধ্যান ধারণা ও চিন্তা ভাবনার ফসল হিসেবে রাষ্ট্রীয় মতবাদ গড়ে উঠে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীকদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে । প্রত্যেক রাষ্ট্রতত্ত্বে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের বিশেষ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক লাস্কি উল্লেখ করেন যে, “কোন রাষ্ট্রতত্ত্বই সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিত ছাড়া বোধগম্য নয়।” রাজনৈতিক দার্শনিক তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। সমকালীন রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা এবং এর প্রতি সমর্থন দান বা প্রত্যাখান কিংবা একে উন্নত করার জন্য বেশীর ভাগ রাষ্ট্রীয় মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইতালীর দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলীর রাজনৈতিক দর্শন বা মতবাদ সমকালীন ইতালীর রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র ।
রাষ্ট্রতত্ত্ব মূলত রাজনৈতিক ঘটনবলীর ব্যাপক, সুবিন্যস্ত ও সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার এক প্রচেষ্টা বিশেষ (Political theory is an attempt to arrive at a comprehensive coherent and general account of political phenomena) রাজনৈতিক সংগঠনের বিবর্তনের ন্যায় রাষ্ট্রতত্ত্বে এক ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাসের গতিধারার সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিবর্তিত হয়। রাষ্ট্রতত্ত্ব রাজনৈতিক ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিজ্ঞান, কৃষ্টি, প্রথা, ধর্ম, সাহিত্য, ঐতিহ্য রাষ্ট্রীয় মতবাদকে প্রভাবিত করে থাকে।
হবস, লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তাঁদের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। আবার একথাও সত্য যে, রাজনৈতিক মতবাদও অনেক সময় রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে উন্নত করে। জন লকের মতবাদ ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে রুশোর মতবাদ।
সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের চিন্তাধারা যখন যুক্তিবাদের পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন থেকে রাষ্ট্রতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার দ্বার উম্মুক্ত হয়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিষ্টটলের যুগ থেকেই রাষ্ট্রতত্ত্বের সুসংঘবদ্ধ ইতিহাস শুরু হয়। তবে এ কথা সত্য, কোন রাষ্ট্রীয় মতবাদ সর্বকালের ও সর্বযুগের জন্য গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিজ্ঞান। সুতরাং এ বিজ্ঞানের কোন মতবাদই পরিবর্তন এবং সংশোধনের উর্ধ্বে নয়। সমাজ বিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা খুব কম ক্ষেত্রেই একমত হতে পারেন। কেননা অবস্থা, পরিবেশ ও রাজনৈতিক সমস্যার ভিন্নতার কারণে মত পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের কার্যাবলী, গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্রমশঃই বিকশিত হচ্ছে।
রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রের উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। আমাদের চিন্তা ও যুক্তিকে সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশের প্রশ্নে ও সঠিক সমাধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রতত্ত্ব আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হেনরী সিজউইক বলেছেন, “রাষ্ট্রতত্ত্বের লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় প্রশ্নগুলোর যুক্তিপূর্ণ সমাধান নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নতুন নতুন কলাকৌশল উপস্থাপন করা নয় বরং যে সকল চিন্তা ধারা ও যুক্তির সাথে আমরা সুপরিচিত সেগুলোকে সুচিন্তিত উপায়ে ও সুবিন্যস্তভাবে পরিবেশন করা।”
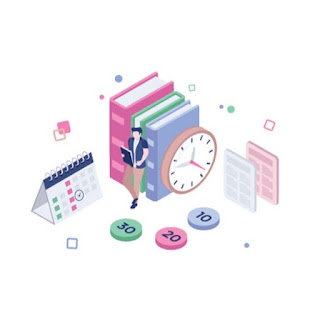
Comments
Post a Comment